প্রাণের ২৫শে' ও একটি নৃত্যানুষ্ঠান ...
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে ॥
হেরো গো অন্তরে অরূপসুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে ॥
চলতি বছর গুরুদেবের জন্মদিনে হঠাৎ ঘটিত কিছু ঐকান্তিক এবং ব্যক্তিগত ইতিহাসের চমকিত সাক্ষী রইলাম, তা না লিখে রাখলে, স্মৃতির প্রতি বঞ্চনা বটে এবং লেখা যে এইভাবে শুরু করব, তা আশাতীতও বটে। জীবনের প্রান্তে, প্রায় আশি বছর বয়সে এক নবীন লেখকের 'আবদারে' গুরুদেব সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা নামক একটি প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন। কৈশোরে সেই লেখাটি পড়ে মনে হয়েছিল জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস পাঠ থেকে সযত্নে আরো একখানি ‘ইতিহাসের’ ইতিহাস রচনা করলেন। এই রচনাটিতে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম উপলব্ধির মাধ্যমে এমন একটি অবয়বের সৃষ্টি করেছিলেন, যার বিশুদ্ধমানীর দ্বারা অন্য একটি ‘ভালো’ মানের পরিচিতি ঘটেছিল আমাদের পাঠ্যে; সেটিতে যথেষ্ট মনোনিবেশ করতে পারিনি তখন, পড়া, বোঝার ভাষা ছিল বেশ, তবু, অবগাহন ছিল জটিল। যা নিতান্ত বালকের প্রাণের কথা, ব্যাকুলতা, অস্ফুট আলোড়ন, অন্তরে, তা সে এক অনন্য স্পর্শের ছোঁয়া --- তাতে সেমিওটিক্স/চিহ্নবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাসের জানার দায় নগণ্য; এই ছোঁয়া আবেগের, শান্তের, ধীরের। প্রায় আশির এক বালকের স্মৃতি খুঁড়ে এক নবীন লেখকের আবদারে যে অন্য দাবী সন্দর্ভ খচিত হয়েছিল, পরবর্তীতে তাকে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধমানীদের তত্ত্ব-তথ্য-শল্যচিকিৎসা অন্য পথে বয়ে চলে। তবে, এর সাথে অজান্তে সেই সব গঠনবাদী বিন্যাস পর্ব পার করে এক অন্য আবেশ ছড়িয়ে পরেছিল ঐকান্তিক, অপর, অন্য রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির । একবার ফিরে যাওয়া যাক সেই রচনাটির জানালায়। দেখা যাক বালকের অপার আনন্দ। বালকের বিস্ময় ---
“ ... আমাদের ব্যবহার গরিবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানা মাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। ... সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম, সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। ”
বালকের এই যে সরল ভাবনার দ্যুতি, সরলতর তার বিস্তার। “শীতবস্ত্র”, “গায়ে”, “একখানামাত্র”, “জামা”, “গরম লেপ” --- ওঁর লেখায় বারে বারে এইরকম ঐকান্তিক কৃচ্ছ্রসাধন ফিরে এসেছে। সেই জানালা জানিনা কেউ খুলে দেখেছিলেন বা দেখছেন অথবা দেখবেন কিনা! তবে যে সত্য তিনি রেখেছেন, “ ... একটি চাওয়া ভিতর হতে/ ফুটবে তোমার ভোর-আলোত/ প্রাণের স্রোতে-- / অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই ...” তার সেই নিবিড় চাহিদা, প্রাণের আনন্দে ভোর-আলোতে রবিচ্ছটায় তিনি নিজেকে একাত্ম হওয়ার মতই শান্ত এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী রইলাম। দৈনন্দিন পড়ালেখা শেষ হতেই, এই প্রাচীন ব্লগ, ফ্লিকার, ও ইউটিউব নিয়েই সময় কাটে, এই যে নচ্ছার সময় ... সারাদিন বাড়িতেই কাটে, জনান্তিকে, আমার ভালোবাসার, ভালো থাকার পরিসর। এই ইউটিউবেই একটি হঠাৎ একপ্রকার দাবী জানিয়ে ফেলেছিলাম। দুই শিল্পীর একটি সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠান দেখে গুরুদেবের জন্মদিন উপলক্ষে একটি 'দাবী' জানিয়ে ফেলেছিলাম, “ ... কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়--পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়, সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি” ছাপিয়ে। বলেছিলাম, “ কবির জন্মদিনে ওঁর রচিত কোনো একটি গানের যদি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন” মন্তব্য করেছিলাম --- সেই নৃত্যশিল্পীদ্বয়ের অনাবিল সম্মতিজ্ঞাপনের প্রশ্রয় -- আমার মত তারাও যে ওঁকে ঈশ্বর মানেন।
আমি লিখলাম,
“ ঈশ্বর! সাধু! সাধু! জাগতিকজ্ঞান হওয়া অবধি তাঁকে এই রূপেই চিনিয়েছিলেন আমার বাবা। "আশ্রম" প্রবন্ধে তিনি উপনিষৎ-এর একটি বাণী তর্জমা করে বলেছিলেন, '... যখন এই দেবতাকে, এই পরমাত্মাকে, এই ভুতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি গোপনে থাকতে পারেন না।... '। আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেহে, মনে যে "গুরুদেব" নাম্নী বিশালতার খানিক পরশ দিয়ে যায়; আবার খানিক শুনিয়ে যায়, ' ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না-- ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে... ' সেই ঈশ্বর কখন আমার প্রেম, কখন যে পূজা, আমাদের ভক্তি, কখন যে বাৎসল্য.. ! তাই বুঝি আমরা গোপনে রাখতে পারি না সেই ঈশ্বরমগ্নতা! অনেক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ। নমস্কার নেবেন। আপনাদের কবি প্রণামের অপেক্ষায় রইলাম।”
এবং তারা অনুষ্ঠান পালন করলেন। তাদের বাড়িতে। অপূর্ব সেই সারল্য। সেই সত্য। সেই রেশে কবির প্রিয় ব্যাক্তিগত ইতিহাস রচিত হল।
২৫শে বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ। অনুষ্ঠানে বালক কবির অতি ক্ষুদ্র চাওয়ার সেই পুরাতন ইতিহাস তারা রচনা করলেন। যা অভুতপূর্ব, অনাস্বাদিত এক বীক্ষাশাস্ত্র। শিক্ষিত হলাম আমি। তারা বালক রবির সকালবেলাকার
এই আনন্দের অভ্যর্থনা নিয়ে আসলেন আমার ২৫শে বৈশাখে। ঈশ্বর সেইদিন তাদের
মাধ্যমেই মুগ্ধ হলেন। ঈশ্বর ঠিক এই রূপেই নেমে আসেন, আসেন।
এইভাবে এক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের, নৃত্যের একান্ত
ইতিহাস। কবির ইচ্ছায় আরেক উত্তর-ইতিহাসও যে এইভাবে রচিত হয় তাই লিখে রাখা।
তাদের আরো লিখলাম,
“মানবত্ত্ববোধের চিন্তন সম্মিলিত এই গানখানি ও আপনাদের অসামান্য নৃত্য। আরতি। আমার নমস্কার নেবেন। অজস্র ধন্যবাদ। “ ...কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ... পূর্বপশ্চিম বন্ধুসঙ্গম মৈত্রীবন্ধন পুণ্যমন্ত্র পবিত্র বিশ্বসমাজে।" তাঁর লেখার পরতে পরতে আজও কত কত সমকালীন অভাবের মুক্তির উপায়... কত যে পরশমণিতে খচিত... কী বা শিখলাম.. "তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ৷ তার অণু-পরমাণু পেল কতই আলোর সঙ্গ, তার অন্ত নাই গো নাই।..." এই ভাবের পাগল হতে আর পারলাম কই! তিনি সর্ব ব্যাপী, সর্বত্র বিদ্যামান। এই জীবনে, তাঁর যে কোন একটি গান, গীতিনাট্য, এমনকি আঁকিবুঁকিও [doodle!] এক এক বয়সে এক এক মূল্যায়নে সমৃদ্ধ করে যায়। বর্তমান নচ্ছার ক্ষণে আপনাদের অনুষ্ঠিত "ধ্বনিল আহবানের" সাথে যে নৃত্য দেখলাম তা গানটির একটি অপর মানে, এক ভিন্ন মুক্তির খোঁজ দিয়ে গেল, যা এক অজানার আস্বাদ। আর এইখানেই গুরুদেব সর্ব কালব্যাপী। ””'
তাঁর এত লেখার দরকার কি প্রয়োজন ছিল?' এমন একটি কথা প্রয়শই শোনা যায় বা জোরালো হয়ে ওঠে সমাজ-মাধ্যমে, এমনকি পত্র-পত্রিকাগুলিতেও, টেবিলচাপড়ানোয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার হুংকার জানায়; ঠিক সেই সময়ে গেয়ে ওঠে, "আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই, তখন যাহা পাই, সে যে আমি হারাই বারে বারে..."। তাঁর প্রতিটি পাতায় কত যে না জানা, না বোঝা অণু-পরমাণু থেকে যায়! আমরা যারা কিছুমাত্র পেলাম তাই নিয়ে বাঁচি। অক্লেশে। 'রবি'তেই বাঁচি আমি। অসামান্য বলেছেন। একটি সমাজ-মাধ্যমও আমায় বেঁধে রাখতে পারেনি। ইয়ুটিউব ছাড়তে পারিনি, প্রাপ্তির পাল্লা ভারি এখানে। এই মাধ্যমেই একটু বলি। বহু বছর পর লিখলাম। হয়ত বেশী। নিজ গুণে মাফ করে দেবেন, " আপ্লুত" দায় নিয়ে, জানি। আমিও যে অভিভূত আপনাদের আমার মন্তব্যটি আনন্দ দিয়েছে।... নমস্কার জানবেন। রবিচ্ছায়ায় থাকুন। ... "
চলবে...
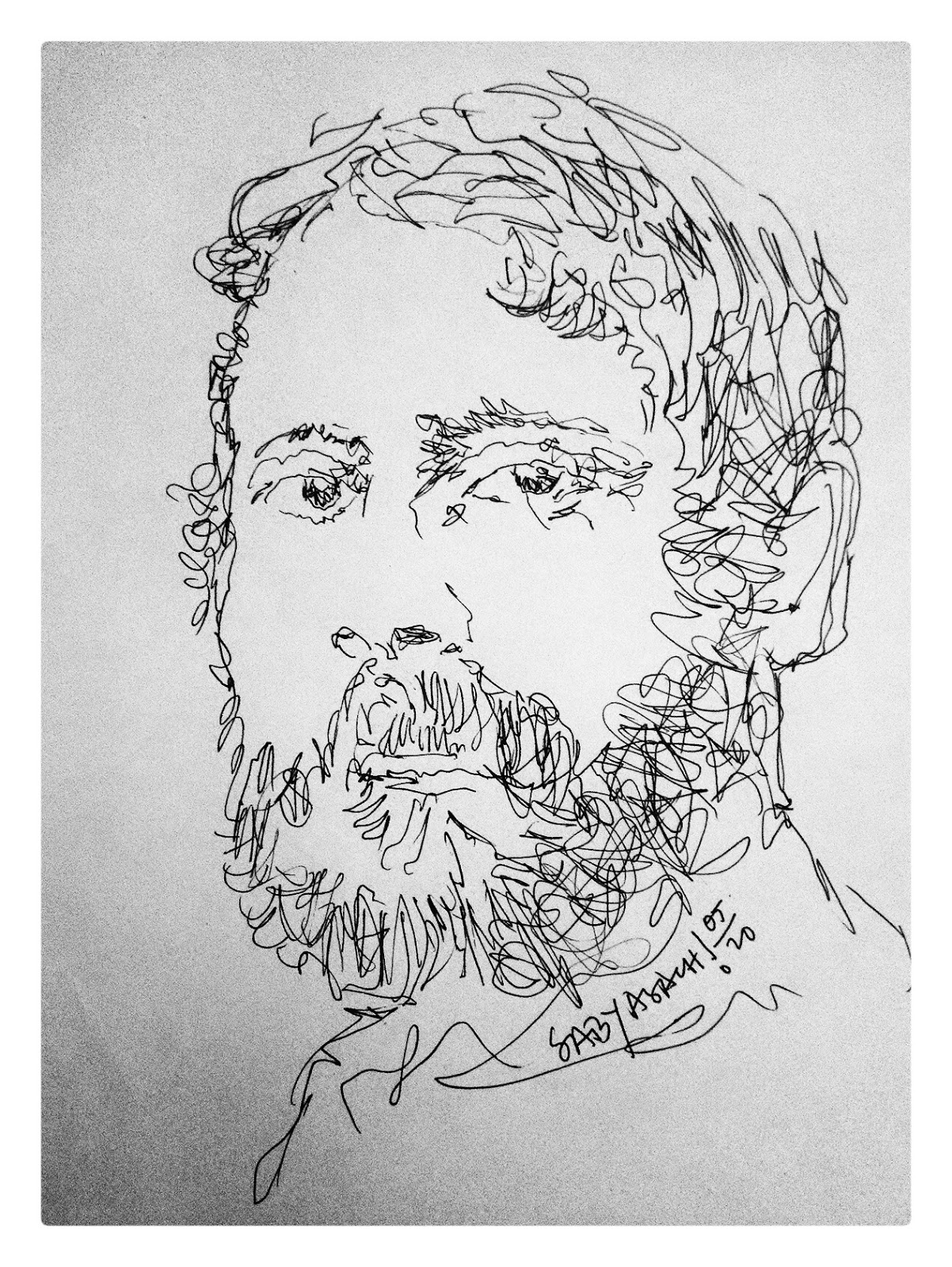

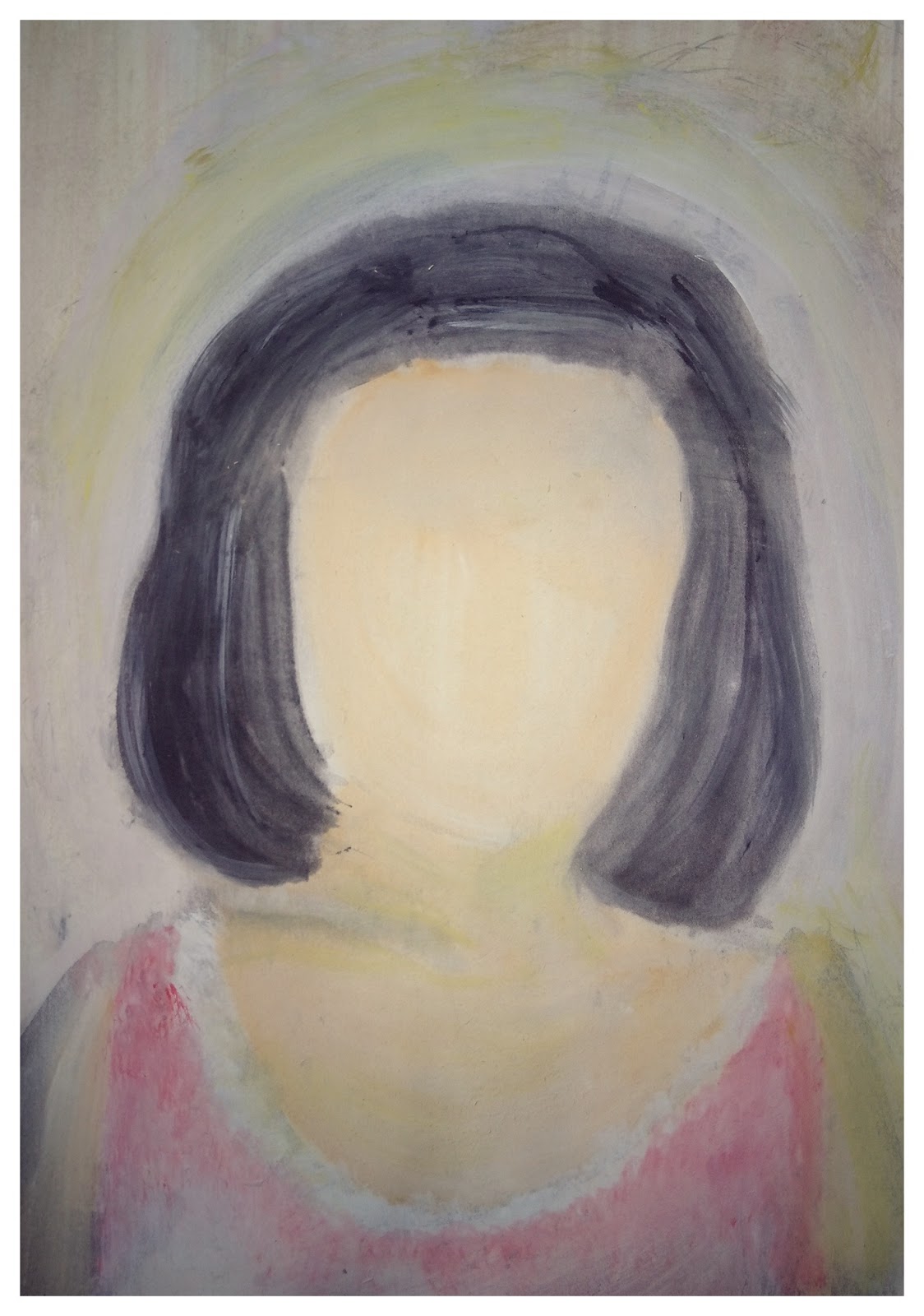
Comments
Post a Comment